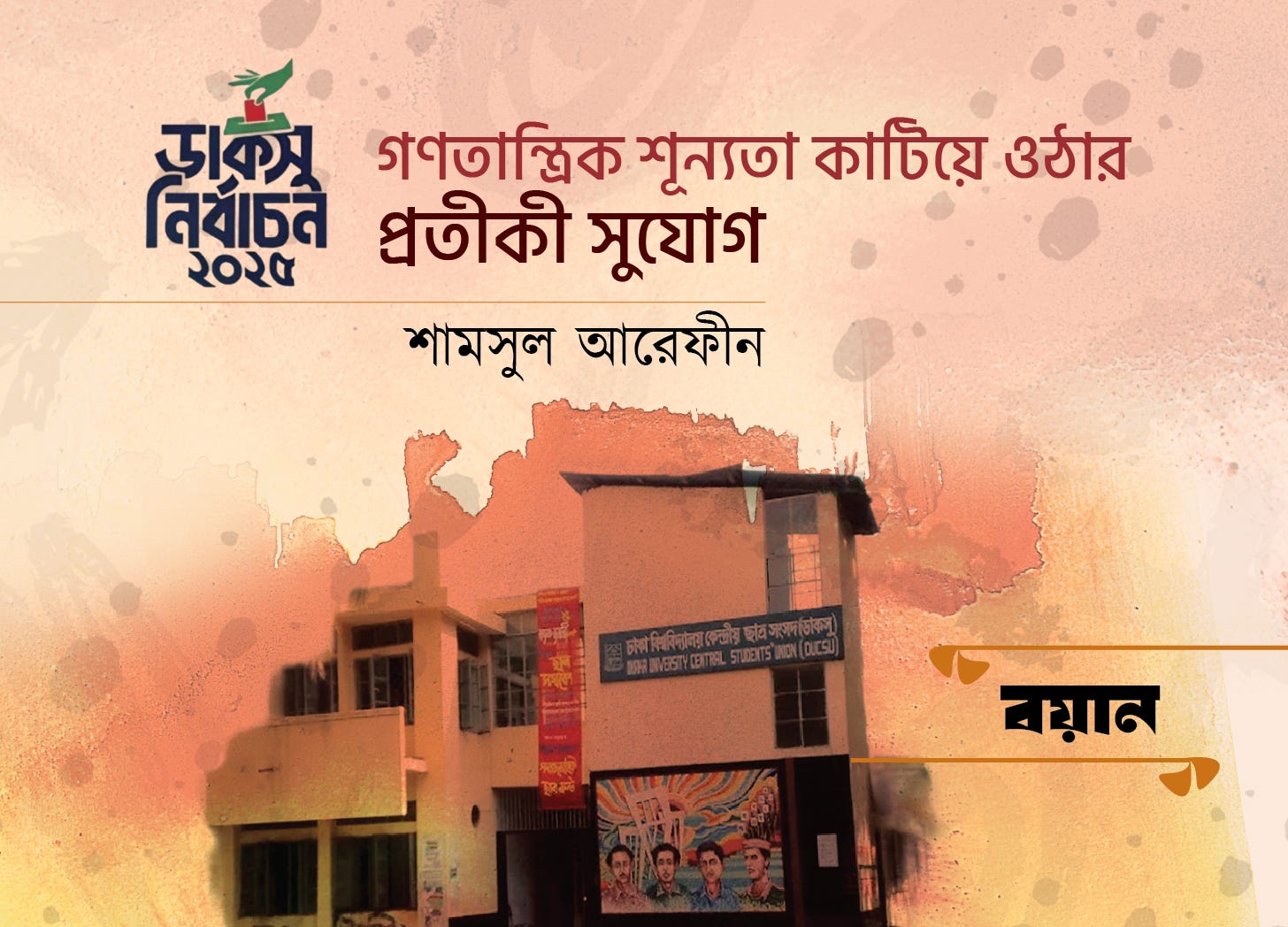ডাকসু নির্বাচন: গণতান্ত্রিক শূন্যতা কাটিয়ে ওঠার প্রতীকী সুযোগ
শামসুল আরেফিন, শিক্ষক ও গবেষক গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
বাংলাদেশে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গণতান্ত্রিক চর্চার যে সংকট চলছিল, জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর তা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। দীর্ঘ দমন-পীড়ন, ভোটবিহীন নির্বাচন এবং একচেটিয়া ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে জাতীয় পর্যায়ে যে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে, সেটি নিছক একটি ক্যাম্পাস নির্বাচনকে ছাড়িয়ে অনেক বড় রাজনৈতিক প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে ডাকসুর নির্বাচন যেন দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে তার একটি পরীক্ষাগার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২০০৯ সালের পর থেকে জাতীয় রাজনীতিতে কার্যত কোনো অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হয়নি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের ভোটে জনগণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এমন এক পরিস্থিতিতে ডাকসুর নির্বাচন গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, গণতন্ত্র কেবল সংসদ বা জাতীয় রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তা চর্চা করতে হয়। ডাকসুর এই নির্বাচন তাই বাংলাদেশের জন্য একটি প্রতীকী “মিনি-পার্লামেন্ট,” যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় ডাকসু ইলেকশন নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে পরীক্ষিত মাধ্যম। ২০১৯ সালে ডাকসুর নির্বাচন হয়েছিল ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে, যা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল কারচুপি ও সন্ত্রাসের কারণে। তবে তবুও সেই নির্বাচনে নতুন কিছু নেতৃত্ব উঠে এসেছিল। যেমন ভিপি নুরুল হক নুর, যিনি পরে জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, কিংবা সাহিত্য সম্পাদক আখতার হোসেন, যিনি আজ নাগরিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে, ডাকসু শুধু ছাত্ররাজনীতির জন্য নয়, জাতীয় নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করে। সুতরাং এবারকার নির্বাচনও ভবিষ্যতের জাতীয় নেতৃত্বের বীজ রোপণের সুযোগ এনে দিয়েছে।
এবারের নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছে যে প্রশাসন আগের তুলনায় নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে চেষ্টা করছে। একটি বড় কারণ হলো—বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায় কোনো রাজনৈতিক দল নেই। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলো আগের মতো ক্যাম্পাস দখল বা ভোট কারচুপির সুযোগ পাচ্ছে না। অবশ্য বাংলাদেশের ভোট সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে জবরদস্তি, সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শন ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু জুলাই-পরবর্তী প্রেক্ষাপট নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যা জাতীয় নির্বাচনের জন্যও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। যদি ডাকসু নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, তবে তা ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের জন্য জনগণের আস্থা পুনর্গঠনে সহায়তা করবে।
গণমাধ্যম ও জনপরিসরেও নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছে। ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে দেশের প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলো অসাধারণ মনোযোগ দিয়েছে। টকশো, রিপোর্ট, জরিপ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নির্বাচনকে জাতীয় আলোচনায় রূপান্তর করা হয়েছে। সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো—প্রার্থীদের উন্মুক্ত বিতর্কে অংশ নিতে হয়েছে, টাউনহলধর্মী সভায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে যেখানে নেতা-জনগণের মধ্যে সরাসরি সংলাপ প্রায় অনুপস্থিত, সেখানে ডাকসুর এই প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে পুনর্গঠনের একটি প্রতীকী ধাপ। তবে উদ্বেগের জায়গা রয়ে গেছে। নির্বাচনী প্রচারণায় আবারও দেখা যাচ্ছে “স্বাধীনতার পক্ষ বনাম বিপক্ষ” বাইনারি। প্রতিপক্ষকে অস্বীকার করার এই রাজনীতি গণতন্ত্রকে দুর্বল করে, কারণ এটি আসলে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির প্রথম ধাপ—যেখানে বিরোধীকে “অন্য” হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে নির্মূল করার চেষ্টা হয়। জাতীয় রাজনীতিতে এই ধরনের বাইনারি বহু বছর ধরে দেখা গেছে; ডাকসু যদি সত্যিই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত খুলতে চায়, তবে এই আদারিং থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি।প্রার্থীরা শুধু দলীয় প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং আমরা কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই—এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ বনাম রাজনৈতিক উৎকর্ষের দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার কাঠামোগত সংকট যেমন শিক্ষক সংকট, গবেষণা তহবিলের অভাব, এবং রাজনৈতিক প্রভাব—ডাকসুর নির্বাচন সেসব প্রশ্নকে আলোচনায় আনার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন ছাড়া গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না।
বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ডাকসুকে ঘিরে জরিপ পরিচালনা করেছে। যদিও স্যাম্পল সাইজ ছোট হওয়ায় জরিপের নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ, তবুও এগুলো জনমত গঠনে প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে সুইং ভোটারদের উপস্থিতি নির্বাচনের ফলাফলকে অনিশ্চিত করে তুলছে। জাতীয় নির্বাচনেও ঠিক একই চিত্র দেখা যেতে পারে—যেখানে আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও যোগ্যতা বড় ভূমিকা রাখবে।
এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের জন্য কেন ডাকসু নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।
ডাকসু নির্বাচন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শিক্ষা ও রাজনীতির কেন্দ্রীয় স্থান। এখানকার ছাত্রসংসদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি পরবর্তী সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে ডাকসুর নির্বাচন প্রতীকী অর্থে জাতীয় রাজনীতির দিকনির্দেশনা বহন করে।ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে ডাকসুর নির্বাচন তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ:
১. বিশ্বাস পুনর্গঠন: দীর্ঘদিনের জালিয়াতিপূর্ণ নির্বাচনের পরে জনগণ যদি ডাকসুতে একটি সুষ্ঠু ভোট দেখে, তবে জাতীয় নির্বাচনে আস্থা ফিরতে পারে।
২. নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্র: এখান থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব ভবিষ্যতের জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে পারে।
৩. গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ: বিতর্ক, উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক প্রচারণা জাতীয় নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে। তবে ডাকসুর নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির সব সংকট সমাধান করতে পারবে না। প্রশাসনের ভূমিকা, ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তঃদ্বন্দ্ব, এবং রাষ্ট্রীয় প্রভাবের বাইরে থেকে একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ। তবুও এটি একটি সূচনা—যেখানে ছাত্ররা নিজেদের ক্ষমতা, কণ্ঠস্বর ও রাজনৈতিক এজেন্ডাকে নতুনভাবে সংগঠিত করার সুযোগ পাচ্ছে।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডাকসুর এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক শূন্যতা ভাঙার প্রতীকী পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু তা নির্ভর করবে নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলকভাবে হয় এবং নির্বাচিত নেতৃত্ব কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার ওপর। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ চালু করা এখন সময়ের দাবি।
ডাকসুর নির্বাচন তাই একটি ইভেন্ট নয়; এটি গণতন্ত্র চর্চার প্রতীক। ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে এটি যেন এক ধরনের গণতান্ত্রিক রিহার্সাল। আমরা যারা দীর্ঘদিন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি, তাদের প্রত্যাশা—এই নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নতুন করে ভাবতে শেখাবে। ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ পূর্ণতা পায় না। ডাকসুর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হয়তো সেই অংশগ্রহণের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে, যা ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের দিকনির্দেশনা দিতে পারে।