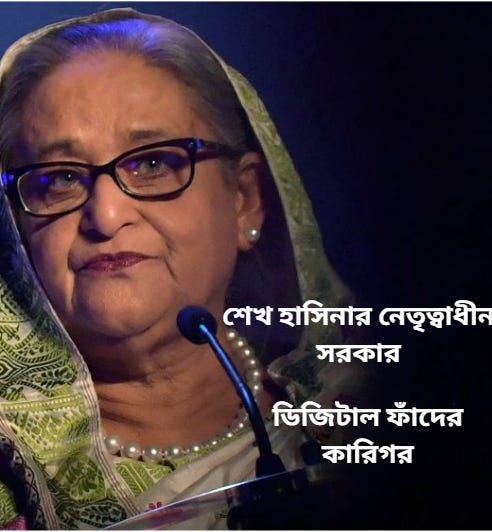বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাঁদ যেভাবে তৈরী হয়েছিল
সায়েম আজাদ
শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে বাংলাদেশ নিঃশব্দে গড়ে তুলেছিল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আক্রমণাত্মক মোবাইল নজরদারি ব্যবস্থা। এর কেন্দ্রে ছিল ইন্টিগ্রেটেড ল’ফুল ইন্টারসেপশন সিস্টেম (আইএলআইএস), যা পরিচালনা করত ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)। সরকারি ভাষায় এটি ছিল “জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার” একটি হাতিয়ার। কিন্তু বাস্তবে এটি পরিণত হয়েছিল এক ব্যাপক নজরদারি যন্ত্রে, যা নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকেই বাধ্য করেছিল নিজেদের ওপর নজরদারির খরচ বহন করতে।
প্রতিটি ফোনকল, প্রতিটি বার্তা, প্রতিটি মেগাবাইট ডেটা, সব কিছুই এই নজরদারি সিস্টেমের মাধ্যমে নকল (ডুপ্লিকেট) করা হতো এবং পুনর্নির্দেশিত (রিরাউট) করা হতো। এই নকল প্রক্রিয়া কিন্তু বিনা খরচে হতো না, এতে অতিরিক্ত ব্যান্ডউইথ লাগত। আর সেই খরচ কে বহন করত? সরকার বা টেলিকম কোম্পানি নয়, বরং সাধারণ ব্যবহারকারীরাই সেই খরচ দিত।
মানুষ ভাবত তাদের মোবাইল ডেটা খরচ বাড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিডিও স্ট্রিমিং, বা অ্যাপ ব্যবহারের কারণে। আসলে প্রতিটি গিগাবাইটের একটি অংশ খরচ হতো এই নজরদারি ব্যবস্থার পেছনে। অর্থাৎ নাগরিকরা আক্ষরিক অর্থেই তাদের নিজস্ব নজরদারির জন্য অর্থায়ন করত, কোনো রকম সম্মতি বা সচেতনতা ছাড়াই।
পশ্চিম ইউরোপে যেখানে একজন ব্যবহারকারী মাসে ১০ গিগাবাইট ডেটাতেই স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারতেন, সেখানে বাংলাদেশে অনেক ব্যবহারকারী ৫০ গিগাবাইট বা তারও বেশি ডেটা ব্যবহার করতেন শুধুমাত্র অনলাইনে উপস্থিত থাকতে। এর কারণ জীবনযাত্রা ছিল না, এটা ছিল নজরদারির কাজে ব্যবহৃত অদৃশ্য খরচ। প্রতিটি বার্তা আটকানো, প্রতিটি সংযোগ নকল করা, প্রতিটি ডেটা রিরাউট করা—সব কিছুর মাধ্যমে নাগরিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক প্রকার “গোপন কর”। গোপনীয়তা তখন পরিণত হয়েছিল লুকোনো ট্যাক্সে।
এখানেই শেষ ছিল না। নজরদারির প্রভাব ফোনের ভেতরেও পৌঁছে যেত।
ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যেত, কারণ ফোনকে বাধ্য করা হতো অতিরিক্ত ট্রান্সমিশন পরিচালনা করতে। নজরদারির পরিকাঠামো ব্যবহারকারীর কাছে বার্তা পৌঁছানোর আগেই সেটি পরিবর্তন করতে পারত, ফলে বিষয়বস্তু বিকৃত হতো।
এভাবে বিশ্বাসের ভিত নড়ে যেত, কারণ ব্যবহারকারীরা নিশ্চিত থাকতে পারত না, তাদের বার্তা গোপন আছে কি না, কিংবা তাদের স্ক্রিনে যা দেখা যাচ্ছে তা আসল কি না। অর্থাৎ ফোন তখন আর তাদের জন্য কাজ করত না; বরং তাদের বিরুদ্ধে কাজ করত।
এই সবই ঘটত এমন এক দেশে, যেখানে কোনো কার্যকর তথ্য সুরক্ষা আইন ছিল না, কোনো স্বাধীন তদারকি সংস্থাও ছিল না। শত কোটি টাকার চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল এই নজরদারি নেটওয়ার্ক, কিন্তু নাগরিকদের জানার কোনো সুযোগ ছিল না, কোন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, কোথায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে, বা কে তার অ্যাক্সেস পাচ্ছে। যখন ডাটাবেস ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল, তখন তারা লক্ষ লক্ষ নাগরিকের রেকর্ড প্রকাশ করেছিল, তবুও জবাবদিহিতার কোনো বালাই ছিল না।
বাংলাদেশের এই ডিজিটাল নজরদারি কেবল নিরাপত্তার জন্য ছিল না, এটিকে নিয়ন্ত্রণের, মুনাফা লাভের এবং মানুষকে চুপ করিয়ে রাখার হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল। উচ্চ ডেটা বিল, দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া ব্যাটারি, বিকৃত তথ্য, সবই নাগরিকদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল “নিরাপত্তা”-র নামে।
কিন্তু প্রকৃত সত্য ছিল—তারা নিজেদের ওপর নজরদারির জন্যই টাকা দিত।
তারা নিজেদের স্বাধীনতা হারানোর জন্য কর দিত। তারা নিজেদের অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাকেই অর্থায়ন করত।
বাংলাদেশ তখন কেবল একটি নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি, এটি পরিণত হয়েছিল নজরদারিভিত্তিক অর্থনীতিতে, যেখানে নাগরিকরা একসঙ্গে পণ্য এবং পেমেন্টকারী, দুটো ভূমিকাতেই বন্দী ছিল। যতদিন না স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আইনি সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ এক এমন ডিজিটাল ফাঁদে আটকে ছিল, যেখানে তাদের গোপনীয়তা, অর্থ এবং যন্ত্র- সবই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতো।