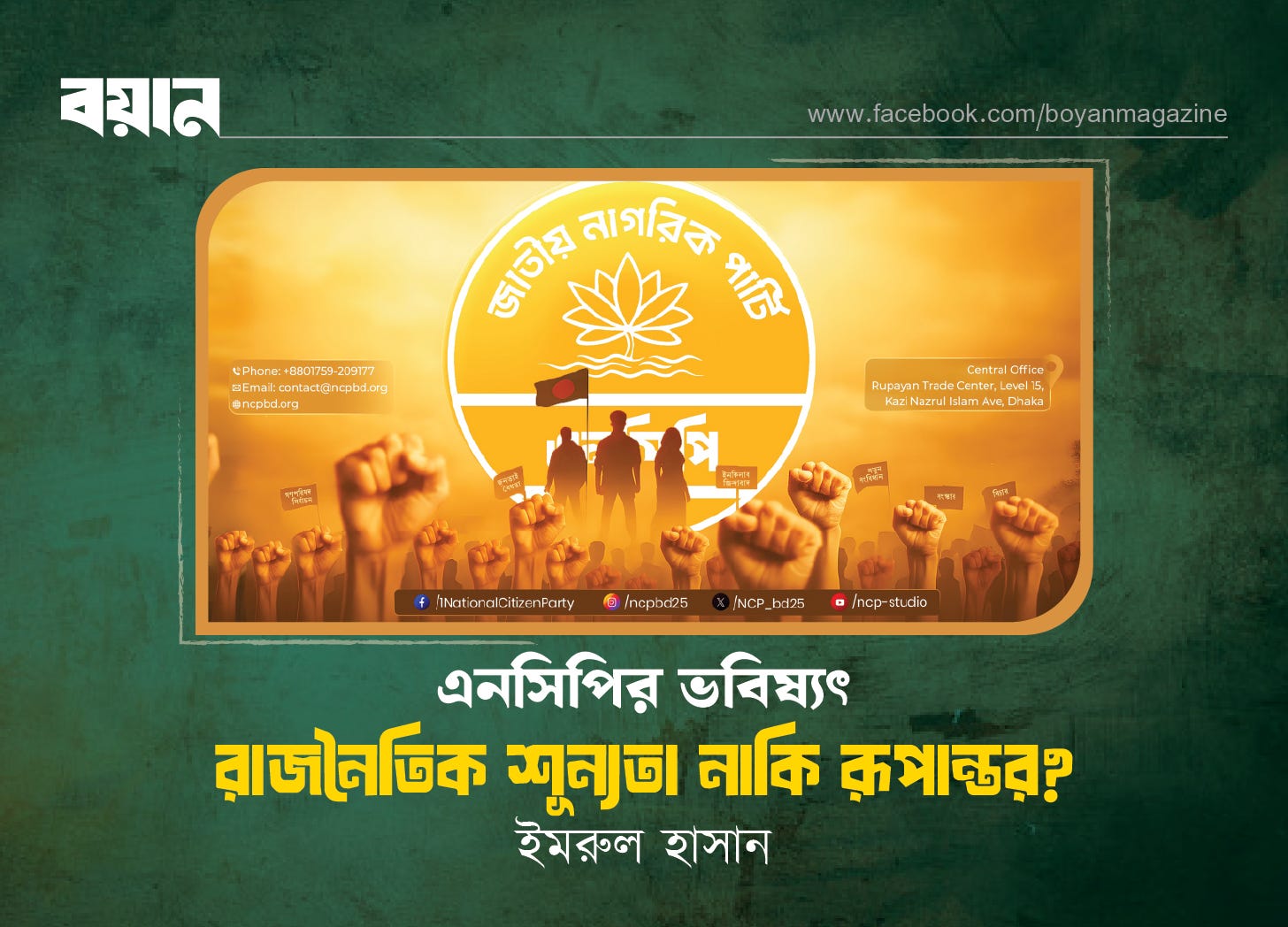এনসিপির ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক শূন্যতা নাকি রূপান্তর?
ইমরুল হাসান, কবি ও চিন্তক
এনসিপি নিয়ে তো হতাশার কথা বলতে চাই না, কারণ তাদের ব্যর্থতা শুধু তাদেরই ব্যর্থতা নয়—বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে এক ধরনের শূন্যতা (ভ্যাকুয়াম) তৈরি হওয়ার ঘটনাই এটি। যার ফলে এনসিপি যে নিজেদের রাজনীতি করতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা সবার জন্যই সমস্যা! কিন্তু রাজনীতিতে আপনি তো কাউকে স্পুন-ফিড করতে পারবেন না; যার যার পার্টি যারা চালাচ্ছেন, তাদেরই নিজেদের জায়গাগুলো ভালোভাবে বোঝার কথা।
আমি বাইরে থেকে দেখি, এখনকার অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তাহলে পরের নির্বাচনের পরে এনসিপি অন্তত চার ভাগে ছড়িয়ে যাবে—
প্রথম গ্রুপ, যারা টাকা–পয়সা কিছু গোছাতে পারবে, তারা রাজনীতি থেকে সরে পড়বে। এবং এটা সবসময়ই হয়। সব টাকা যে আওয়ামি লীগের লোকজন মেরেছে, তা নয়; অনেকেই টাকা মেরে সরে গেছে। এই ধরনের সুবিধাবাদী লোকজন সব দলে, সব সময়ই থাকে। এই ছোটখাট গ্রুপটাই সবচেয়ে আগে হাওয়া হয়ে যাবে। মানে, রাজনীতিতে তাদের আর পাওয়া যাবে না।
দ্বিতীয় গ্রুপ আসলে অন্য দলগুলোর সঙ্গে মিশে যাবে। মোটামুটি একটা অবস্থানে আসার পরে বিএনপির সঙ্গেই অনেকে আলোচনা (নেগোশিয়েট) করবে, বা বিএনপিও হয়তো কাউকে কাউকে নিতে চাইবে। এইভাবে কেউ কেউ রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নেবে হয়তো।
তৃতীয় গ্রুপ হতাশ হয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেবে, বিদেশ চলে যাবে, ক্লান্ত হয়ে যাবে। কেউ হয়তো অ্যাক্টিভিস্ট–ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে থাকবে, কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি করার চাপ আর নিতে চাইবে না।
তবে আমি আশা করি, চতুর্থ গ্রুপ হিসেবে কিছু মানুষ হয়তো থেকে যাবেন, যারা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন—নানান ধরনের অ্যালায়েন্স ও নতুন ফর্মুলেশনের ভেতর দিয়ে নতুন একটা রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে।
কিন্তু মনে হয়, পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এই জায়গাগুলো আলাদা করার ক্ষমতা এনসিপির ভেতরে এখনও তৈরি হয়নি।
তবে একটা রাজনৈতিক শূন্যতা যে আছে, সেটা সত্য। এই মুহূর্তে বিএনপি, জামাত বা এমনকি এনসিপিও সেই শূন্যতা পূরণের অবস্থানে নেই। খেয়াল করে দেখবেন, এ.কে. ফজলুল হক কৃষক–প্রজা পার্টি তৈরি করার আগে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক এজেন্সিও কিন্তু ওইভাবে তৈরি হয়নি।
মানে, রাজনৈতিক শূন্যতা আছে বলেই কেউ সেটা সংগঠিত শক্তিতে রূপ দিতে পারছে—এটা সবসময় হয় না। অনেক সময় অনেকটা সময় লাগে, অথবা জায়গাগুলো রূপান্তরিত হয়। দেখা যাক, কী হয়…